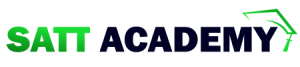Summary
গুপ্ত শাসনের পূর্বে প্রাচীন বাংলার রাজ্যশাসন পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তখন কৌম সমাজ ছিল প্রধান, আর রাজত্ব ও রাজা ছিল না। কৌমের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা ছিল, যেখানে নির্বাচিত নেতা স্থানীয় শাসনের নেতৃত্ব দিতেন। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের আগে রাজতন্ত্রের সৃষ্টি হয়।
গুপ্ত শাসনে বাংলার সঠিক শাসন পদ্ধতির বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলার একটি বৃহত্তর অংশ মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। মৌর্য শাসন পুণ্ড্রনগর থেকে পরিচালিত হতো। গুপ্ত শাসনাধীন অংশগুলো প্রশাসনিক বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হত, যেখানে প্রধান বিভাগ ছিল 'ভুক্তি'। প্রতিটি ভুক্তিতে বিষয় ও মণ্ডল ছিল এবং গ্রাম ছিল সর্বাধিক মৌলিক প্রশাসনিক একক।
ষষ্ঠ শতকে গুপ্তবংশের পতনের পর বঙ্গ একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় সামন্ত রাজাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তারা 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করতেন। পাল বংশের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলার শাসন ব্যবস্থায় নতুন যুগ শুরু হয়, যেখানে রাজত্বের অধিকাংশ দায়িত্ব ছিল রাজার ওপরে।
রাজ্যশাসনে রাজা, মন্ত্রী ও অমাত্যগণ সহায়তা করতেন। আয়-ব্যয়ের জন্য বিভিন্ন রাজস্ব উৎস ছিল, প্রধানত কর ধার্য করা হতো উৎপন্ন শস্যের ওপর। রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। শান্তি রক্ষার জন্য বিচার ও পুলিশ বিভাগ ছিল এবং সামরিক বাহিনীও সংগঠিত ছিল। সামন্তদের বিনা অনুমতিতেও স্বাধীনতা ঘোষণা করার উদাহরণ ছিল।
মোটামুটি, প্রাচীন বাংলার শাসন পদ্ধতি ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় পিছিয়ে ছিল না।
গুপ্ত শাসনের পূর্বে প্রাচীন বাংলার রাজ্যশাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে সঠিক কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না । এদেশে গুপ্ত শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে কৌম সমাজ ছিল সর্বেসর্বা । তখন রাজা ছিল না, রাজত্ব ছিল না । তবু শাসন-পদ্ধতি সামান্য মাত্রায় ছিল । তখন মানুষ একসাথে বসবাস করত । কৌমদের মধ্যে পঞ্চায়েতী প্রথায় পঞ্চায়েত দ্বারা নির্বাচিত দলনেতা স্থানীয় কৌম শাসনব্যবস্থায় নেতৃত্ব দিতেন । বাংলার এ কৌম ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হয়নি । খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্বেই বাংলায় কৌমতন্ত্র ভেঙে গিয়ে রাজতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল । গুপ্তদের সময় বাংলার শাসন-পদ্ধতির পরিষ্কার বিবরণ পাওয়া যায় । আনুমানিক দুই-তিন শতকে উত্তরবঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বাংলায় মৌর্য শাসনের কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রনগর-বর্তমান বগুড়ার পাঁচ মাইল দূরে মহাস্থানগড়ে। অনুমান করা হয় ‘মহামাত্র' নামক একজন রাজ প্রতিনিধির মাধ্যমে তখন বাংলায় মৌর্য শাসনকার্য পরিচালিত হতো। বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হলেও সমগ্র বাংলা গুপ্ত সম্রাটদের সরাসরি শাসনে ছিল না । বাংলার যে অংশ গুপ্ত সম্রাটদের সরাসরি শাসনে ছিল না তা ‘মহারাজা' উপাধিধারী মহাসামন্তগণ প্রায় স্বাধীন ও আলাদাভাবে শাসন করতেন । এ সকল সামন্ত রাজা সব সময় গুপ্ত সম্রাটের কর্তৃত্বকে মেনে চলতেন । ধীরে ধীরে বাংলার সর্বত্র গুপ্ত সম্রাটদের শাসন চালু হয়। এ মহাসামন্তদের অধীনে বহু কর্মচারী নিযুক্ত থাকতেন ।
বাংলাদেশের যে অংশ সরাসরি গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে ছিল তা কয়েকটি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত ছিল । এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় বিভাগের নাম ছিল 'ভুক্তি' । প্রত্যেক 'ভুক্তি' আবার কয়েকটি বিষয়ে, প্রত্যেক বিষয় কয়েকটি মণ্ডলে, প্রত্যেক মণ্ডল কয়েকটি বীথিতে এবং প্রত্যেকটি বীথি কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত ছিল । গ্রামই ছিল সবচেয়ে ছোট শাসন বিভাগ । গুপ্ত সম্রাট নিজে ভুক্তির শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন । কোনো কোনো সময় রাজকুমার বা রাজপরিবার থেকেও ভুক্তির শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হতো। ভুক্তিপতিকে বলা হতো ‘উপরিক'। পরবর্তী সময়ে শাসকগণ 'উপরিক মহারাজ' উপাধি গ্রহণ করতেন। সাধারণত 'উপরিক মহারাজ’-ই তার বিষয়গুলোর শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন । কিন্তু কোনো কোনো সময়ে সম্রাট নিজে তাদের নিয়োগ করতেন । গুপ্তযুগের ভুক্তি ও বিষয়গুলোকে বর্তমান সময়ের বিভাগ ও জেলার সাথে তুলনা করা যেতে পারে ।
ষষ্ঠ শতকে উত্তর-পশ্চিম বাংলায় গুপ্তবংশের শাসন শেষ হয়ে যায়। বঙ্গ স্বাধীন ও আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে । তখন বঙ্গে যে নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা মূলত গুপ্ত আমলের প্রাদেশিক শাসনের মতোই ছিল । গুপ্তদের সময়ে রাজতন্ত্র ছিল সামন্তনির্ভর । এ আমলে তার পরিবর্তন হয়নি । বরং সামন্ততন্ত্রই আরও প্রসার লাভ করেছে । গুপ্তরাজাদের মতো বাংলার সামন্ত রাজাগণও 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করতেন । এরাও বিভিন্ন শ্রেণির বহুসংখ্যক রাজকর্মচারী নিয়োগ করতেন । পাল বংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে নতুন যুগের শুরু হয় । পাল বংশের চতুর্থ শতকের রাজত্বকালে বঙ্গে তাদের শাসন-ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পূর্বের মতো পাল যুগেও শাসন-ব্যবস্থার মূল কথা হলো রাজতন্ত্র । কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ছিলেন রাজা স্বয়ং। রাজার পুত্র রাজা হতেন। এ নিয়ম থাকা সত্ত্বেও ভ্রাতা ও রাজ পরিবারের অন্যান্য নিকটাত্মীয়ের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ ও সংঘর্ষ হতো । এ সময় থেকে সর্বপ্রথম একজন প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান সচিবের উল্লেখ পাওয়া যায় । তিনি ছিলেন সর্বপ্রধান রাজকর্মচারী ।
রাজ্যের সকল প্রকার শাসনকার্যের জন্য কতকগুলো নির্দিষ্ট শাসন-বিভাগ ছিল। এর প্রতিটি বিভাগের জন্য একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকতেন । রাজা, মন্ত্রী ও অমাত্যগণের সাহায্যে কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনা করতেন। পিতা জীবিত থাকলেও অনেক সময় যুবরাজ শাসনকার্য পরিচালনা করতেন । কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের বিভিন্ন উৎস ছিল । এর মধ্যে নানা প্রকার কর ছিল প্রধান । উৎপন্ন শস্যের ওপর বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য হতো। যেমন—ভাগ, ভোগ, হিরণ্য, উপরি কর ইত্যাদি । কতকগুলো উৎপন্ন দ্রব্যের এক ষষ্ঠমাংশ রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হতো । দস্যু ও তস্করের ভয় থেকে রক্ষার জন্য দেয় কর, ব্যবসায়-বাণিজ্য শুল্ক, খেয়াঘাট থেকে আদায়কৃত মাশুল ইত্যাদি ছিল সরকারের আয়ের কয়েকটি উৎস । বনজঙ্গল ছিল রাষ্ট্রের সম্পদ । সুতরাং এটিও রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি অন্যতম উৎস ছিল ।
বিভিন্ন রকমের রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। রাজস্ব আয়-ব্যয়ের হিসাব ও দলিল বিভাগ দেখাশুনা করার ব্যবস্থা ছিল । ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ঠিক করার জন্য জমি জরিপের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো । মুদ্রা এবং শস্যের আকারে রাজস্ব আদায় হতো । পাল রাজাদের সময়ে শান্তি রক্ষার জন্য সুন্দর বিচার ও পুলিশ বিভাগ ছিল। এ সময়ে গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর বাহিনী ছিল । পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তী ও রণতরী- এ চারটি বিভাগে সামরিক বাহিনী বিভক্ত ছিল । গুপ্তদের মতো পালদের সময়েও সামন্ত রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের নানা উপাধি ছিল । কেন্দ্রীয় শাসনের শৌর্য ও বীর্য সামন্তদের অধীনতায় থাকতে বাধ্য করতো। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে এরা স্বাধীনতা ঘোষণা করতো। পাল শাসকদের শক্তি অনেকাংশে এরূপ সামন্তরাজদের সাহায্য ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করত। পাল রাজ্যে যে শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল তা পরবর্তী সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ ও সেন রাজত্বকালে রাষ্ট্র শাসনের আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে । এ সময়ে রানিকে রাজকীয় মর্যাদা দেয়া হয়েছে। শাসনকার্যে যুবরাজদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল । জ্যেষ্ঠ রাজকুমার যুবরাজ হতেন। মোটামুটিভাবে এই ছিল প্রাচীন বাংলার শাসন পদ্ধতি। পণ্ডিতদের মতে, শাসন পদ্ধতির ব্যাপারে বাংলাদেশ সে সময়ে ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় মোটেই পিছিয়ে ছিল না ।
Read more